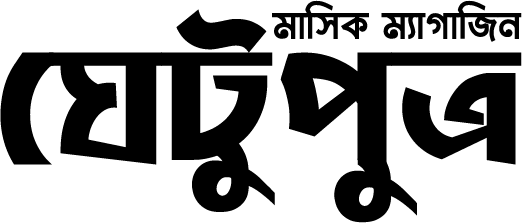ডিসেনসিটাইজেশন, সমকামিতা আর পেডোফিলিয়া
Share

ফোবিয়া হচ্ছে যখন কারও স্বাভাবিক কোন কিছু সম্পর্কে অস্বাভাবিক পরিমান ভয় থাকে। উচ্চতা, মাকড়শা, সাপ, বদ্ধঘর এগুলোকে হয়তো অনেকে অপছন্দ করেন, কিন্তু যাদের ফোবিয়া থাকে, তারা বদ্ধঘরে অক্সিজেনের অভাব হওয়ার আগেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, সামান্য উচ্চতাতেই হাত পা কাপাকাপি শুরু করে দেন, ছোট, নিরীহ প্রকৃতির মাকড়শা দেখেও ভয়ে জমে যান। ফোবিয়া দূর করার জন্য মনোবিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটা ভিন্ন পথে আগান, যার একটা হচ্ছে ‘এক্সপোজার থেরাপী’। যার উচ্চতার ভয়, তাকে প্রথমে এক তলা, তারপর দো’তালা, তারপর আরেকটু উঁচু জায়গায় নিয়ে আস্তে আস্তে বুঝতে দেয়া যে উঁচুতে উঠলেও আসলে কিছু হয় না, জিনিসটা খুবই স্বাভাবিক। এই যে আস্তে আস্তে এক্সপোজ করে অস্বাভাবিক একটা ভয়কে স্বাভাবিক করে আনা হয়, একে বলা হয় ‘ডিসেনসিটাইজেশন’।
ডিসেনসিটাইজেশন যেমন মানসিক অসুস্থতা সারাতে থেরাপি হিসেব কাজ করে, তেমনি ভিন্ন ধরণের ডিসেনসিটাইজেশন সুস্থ মানুষকেও মানসিক ভাবে অসুস্থ করে দিতে পারে। এই ডিসেনসিটাইজেশন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে আর্মিকে ট্রেইনিং দেয়া হয়। যেই ছেলেটা মাত্র আর্মিতে ঢুকেছে, তার হাতেই চাবুক তুলে দিলে সে ইন্টারোগেশনের সময় সেটা ব্যবহার করতেই পারবে না। তাই আমেরিকানরা একটা দারুণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। আর্মিতে আসা নতুনদের ইন্টারোগেশন রুমের দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতো, ভিতরে সিনিয়ররা ঝাল মিটিয়ে রক্তারক্তি করে ইন্টারোগেইট করতো। বাইরে বসে থাকা নতুনেরা শুধু সেটা শুনতো। পরের দিন, শোনার পাশাপাশি, বাইরে থেকেই দেখার ব্যবস্থা হয়ে যেত। এরপর যখন ওদের হাতে চাবুক তুলে দেয়া হতো, তখন ওরা খুব সহজেই রক্তারক্তি করতে পারত।
রিসার্চে দেখা গিয়েছে যেসব শিশুরা এমন ভিডিও গেইম খেলে যেখানে মারামারি, রক্তারক্তি বেশি, সেই সব শিশুরা আস্তে আস্তে সেগুলোকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। তখন খেলার মাঠে কাউকে পছন্দ না হলে ঘুষি দিয়ে নাক ফাটিয়ে দেয়া তার কাছে কেবল স্বাভাবিকই মনে হয় না, উচিত বলে মনে হয়।
একটা সময় ছিল, খুব বেশি আগে না, একশ-দেড়শ বছর আগেই বিয়ের আগে প্রমিকার হাত ধরতে পারাই ছিল বিরাট ব্যাপার। জেইন অস্টেনের ‘এমা’ পড়তে গিয়ে চমকে উঠেছিলাম, যখন পড়লাম মিস্টার এলটন ঘোড়ার গাড়িতে ‘মেইড ভায়োলেন্ট লাভ টু এমা’। পরে টিচার বুঝিয়ে দিলেন, মিস্টার এলটন জেইনের হাত ধরে প্রেম নিবেদন করেছিল। মাত্র দেড়শ বছরেই মেইকিং ভায়োলেন্ট লাভের সংজ্ঞায় অস্বাভাবিক রকমের পরিবর্তন। উদাহরন দিলাম জেইন অস্টেনের, সেটা মনে আছে বলে, কিন্তু মাত্র একশ বছর আগের শরৎচন্দ্রের সাহিত্যেও থীমটা ওরকমই। মুসলিম সাহিত্যিকদের সাহিত্যে তো ব্যাপারগুলো আরও সিরিয়াস ছিল।
মাত্র একশ বছরে পৃথিবীর কি ভীষণ পরিবর্তন। এর কিছু কিছু হয়তো দরকার ছিল, কিন্তু মানুষ সীমারেখাগুলো ধাক্কা দিয়ে সরাতে সরাতে এখন এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যে সীমারেখাগুলো এখন কনফিউজিং।
যেই বাবা মায়েরা বিয়ের আগে হাত ধরার অধিকার নিয়ে যুদ্ধ করেছিল, তারা হঠাৎ করে টের পেল, তাদের ছেলেমেয়েরা বিয়ের আগে সঙ্গী/সঙ্গিনীর পুরাটুকুই উপভোগ করার অধিকার চায়। আর যেই বাবামায়েরা বিয়ের আগে সঙ্গী সঙ্গিনীর পুরাটুকুই উপভোগ করেছিল, তারা হঠাৎ টের পেল, তাদের ছেলেমেয়েরা আর বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আগ্রহী নয়।
এই সামাজিক আন্দোলনগুলো খুব কাছাকাছি হয়েছে। যেহেতু এই সীমারেখা নির্ধারনের একমাত্র একক ছিল মানুষের গণমত, সে জন্য মানুষের গণমত বদলানোর সাথে সাথে এই সীমারেখাগুলো বদলানো কেবল সময়ের ব্যাপার।
সমকামিতার ইতিহাস খুবই ইন্টারেস্টিং। আর একশ বছর আগেও সমকামিতা যে কি জিনিস, এবং সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যে এরকম করতে পারে, সেটা সাধারন মানুষেরা চিন্তাও করতে পারতো না। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় সমকামিতা নিয়ে একটু একটু লেখালেখি শুরু হলো, এবং সেটা থামলো না। আস্তে আস্তে সমকামীদের আন্দোলনের জন্য সমকামিতার যেটা আমার কাছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগে সেটা হচ্ছে, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সমকামিতা মনোবিজ্ঞানীদের জন্য তৈরি করা মানসিক অসুস্থতার লিস্ট আইসিডি-৯ এ ছিল, অর্থ্যাৎ ১৯৯০ সাল পর্যন্ত, মাত্র ২০ বছর আগ পর্যন্ত সমকামিতাকে মানসিক অসুস্থতা হিসেবে গণ্য করা হতো। এরপর ক্লাসিফিকেশনটা বদলানো হয়েছে গণমতের চাপে পড়ে।
এরপরে শুরু হলো অদ্ভূত সব ব্যাপার। মানুষ বিয়ে করে, ২/৩ বাচ্চার বাবা মা হয়ে হঠাৎ করে বলা শুরু করলো, এখন আর সে নিজের স্বামী/স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ নয়, তার সমকামিতার আগ্রহ হচ্ছে। এরকম খবর এখনও পর্যন্ত পত্রিকায় আসছে প্রায়েই, তাই গুগল সার্চ করলেই পাবেন অনেক খবর। সমকামিতা থেকে সমস্ত ট্যাবু উঠানোর আইনী ব্যবস্থা নেয়া হলো। ১৯৮০ সালের আমেরিকাতেও মাত্র ৩৪% মানুষ ভাবতো, সমকামিতা (নিজের জন্য না হলেও অন্য মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে) গ্রহনযোগ্য একটা জীবন পদ্ধতি। এখন সংখ্যাটা আরও অনেক বড়। এখন সমকামিতার কনফেশন মোটামোটি একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
এত কথা বলার কারণ সমকামিতা নিয়ে কথা বলা না, যৌনতা নিয়ে আমাদের সামগ্রিক ডিসেনসিটাইজেশন নিয়ে বলা। কখনও ভেবেছেন, আমরা নিজেরাই যেই সীমারেখা নিজ হাতে দূরে ঠেলছি, বড় করছি, এর পরিনতি কোথায়, শেষ কোথায়?
চিন্তাগুলো আসলো, চার্চের শিশু যৌন নির্যাতনের খবরগুলো পড়তে গিয়ে। পেডোফিলিয়া জিনিসটা এত জঘন্য, যে আমি খবরগুলো প্রথম দিকে এড়িয়ে চলছিলাম। এখন দেখলাম, ইস্যুটা পোপ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, তাই পড়তে পড়তে বেশ কিছু উদ্ভট খবরের মুখোমুখি হলাম। একটা হচ্ছে, ২০০৩ সালে আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সম্মেলনে আমেরিকার বড় সড় মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ এক পরশ বিতর্ক হয়ে গিয়েছে, ‘পেডোফিলিয়া’ কে কি মানসিক অসুস্থতা হিসেবে রাখা হবে, নাকি হবে না, সেই নিয়ে। আমি খবরটা পড়ে কিছুক্ষন থ’ মেরে বসে থাকলাম। এও সত্যি হতে পারে! পেডোফিলিয়া, ছোট ছোট নিষ্পাপ শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন মানসিক অসুস্থতা নাকি সুস্থতা, সেটা নিয়েও মানুষ ‘বিতর্ক’ করতে পারে? এটা কি সত্যিই সম্ভব? চোখের সামনে ভেসে উঠলো অসংখ্য খবর, বেশ কিছু মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কখনও নিজের বাবা, কখনও চকলেটের লোভ দেখিয়ে প্রতিবেশী, কখনও চার্চের প্রিস্ট, নিষ্পাপ শিশুদের টলটলের মনের সুযোগ নিয়ে সারা জীবনের জন্য ক্ষত সৃষ্টি করে দেয় ওদের মনে। একদিনের অল্প কিছু সময়ের জন্য এক এক জন মানুষের সারা জীবন বদলে গিয়েছে। হয় তারা নিজেরাই অসুস্থ হয়ে গিয়েছে, না হলে অস্বাভাবিক সব ফোবিয়ায় ভুগেছে। এই পেডোফিলিয়া মানসিক অসুস্থতা কি না, সেটাও বিতর্কের বিষয় হতে পারে?
তারপর মনে হলো, এটা হয়তো শুরু। ঠিক যেভাবে সমকামিতার আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এখনও বোধ হয় তাই হচ্ছে…
খুব ভয় হলো আমার, আমরা কি ভয়ংকর একটা পৃথিবী তৈরি করছি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, যেখানে ওভার এক্সপোজারের জন্য অসুস্থ একদল চরম ডিসেনসিটাইজড মানুষ থাকবে কেবল, যাদের কাছে কোন সীমারেখাই অর্থবহ হবে না, কোন বিকৃতিই আর বিকৃতি থাকবে না…